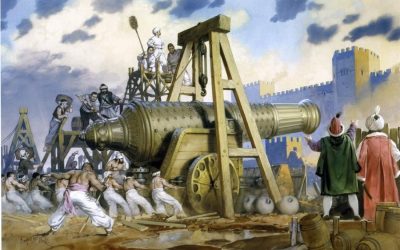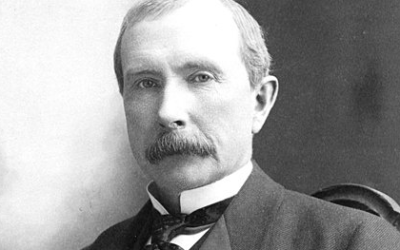পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি বাংলাদেশের সমসাময়িক রাজনৈতিক ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এটি শুধু একটি রাজনৈতিক সমঝোতা নয়, বরং রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে দীর্ঘদিন ধরে চলমান জাতিগত ও আঞ্চলিক সংঘাত নিরসন উপলক্ষে নেওয়া এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।
১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির (জেএসএস) মধ্যে এ চুক্তি সম্পাদিত হয়, যাকে দেশের স্বাধীনতার পর থেকে টানা দুই দশক ধরে পাহাড়ি অঞ্চলে চলমান সশস্ত্র সংঘাত এবং সহিংসতার একটি রাজনৈতিক সমাধান হিসেবে দেখা হয়।
কিন্তু প্রায় দুই দশকেরও বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও এ চুক্তি আজও পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়িত হয়নি, যারফলে আজও পাহাড়ি অঞ্চলে বিভিন্ন ধরণের জাতিগত সংঘাত, নিরাপত্তাহীনতা এবং অস্থিরতা চরমমাত্রায় বিরাজ করছে।
চুক্তির প্রেক্ষাপট বোঝার জন্য এর পূর্ববর্তী পরিস্থিতি বিবেচনায় আনা অতীব জরুরি। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের সংবিধানে “জাতিগত” বা “আদিবাসী” পরিচয়ের স্বীকৃতি না থাকায় পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনগোষ্ঠী নিজেদের বঞ্চিত ও বৈষম্যের শিকার মনে করে।
১৯৭২ সালে মণি সিংহ ও মণি স্বপন দেওয়ান প্রমুখ এ বিষয়ে সরকারের কাছে দাবি জানালেও তা উপেক্ষিত হয়। ফলে ১৯৭২ সালের মধ্যেই মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে গঠিত হয় জনসংহতি সমিতি, যারা পরবর্তীতে পাহাড়ি যুবকদের মাধ্যমে গড়ে তোলে সশস্ত্র সংগঠন “শান্তি বাহিনী”। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কেন্দ্র থেকে বঞ্চনা, ভূমি অধিকার সংকট, সেনাবাহিনী প্রেরণ, এবং সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের অস্বীকৃতি; এসব কারণে সশস্ত্র সংঘাত ধীরে ধীরে তীব্র আকার ধারণ করে।
১৯৭৭ সাল থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে জরুরী পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য ব্যাপকভাবে সেনাবাহিনী মোতায়েন শুরু হয়, এবং টানা প্রায় দুই দশক ধরে এই অঞ্চল কার্যত সামরিক শাসনের আওতায় চলে আসে।
১৯৯০ এর দশক পরবর্তী বিশ্ব রাজনীতির প্রেক্ষাপট, বাংলাদেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা, এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থার চাপ; এসব বিষয় সরকারকে রাজনৈতিক সমাধানের পথে এগিয়ে যেতে বাধ্য করে। দীর্ঘ আলোচনার পর ১৯৯৭ সালে ২রা ডিসেম্বর চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
এ চুক্তির মূল বিষয়বস্তু ছিল পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও জেলা পরিষদের ক্ষমতা বৃদ্ধি, ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য কমিশন গঠন, স্থানীয় প্রশাসনে পাহাড়িদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ, সেনা ক্যাম্প প্রত্যাহার, শরণার্থীদের পুনর্বাসন এবং জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র কার্যক্রমের অবসান ঘটানো।
তবে চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে একাধিক সীমাবদ্ধতা রয়ে গেছে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীদের মতে। তাদের মতে, একদিকে সেনাবাহিনীকে পাহাড়ি অঞ্চল থেকে সম্পূর্ণ প্রত্যাহার না করে “সামরিক নিরাপত্তা” বজায় রাখার কথা বলা হয়, অন্যদিকে ভূমি কমিশন কার্যকরভাবে কাজ শুরু করতে পারেনি। এখনো অনেক পাহাড়ি পরিবার তাদের জমি ফেরত পায়নি এবং এ কারণে তারা পাহাড়ি বাঙালিদের (তাদের মতে সেটেলার, যারা বাইরে থেকে এসে বসতি স্থাপন করেছে) দায়ী মনে করে।
আঞ্চলিক পরিষদের কাঠামো ও ক্ষমতা সীমিত রয়ে গেছে, ফলে স্থানীয় জনগণ প্রত্যাশিত স্বশাসন পায়নি। উপরন্তু চুক্তিকে কেন্দ্র করে পাহাড়ি রাজনৈতিক নেতৃত্বের মধ্যেও বিভাজন সৃষ্টি হয়; একদিকে জনসংহতি সমিতি চুক্তি বাস্তবায়নের পক্ষে কাজ করে, অন্যদিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম গণতান্ত্রিক পার্টি (ইউপিডিএফ) চুক্তিকে অসম্পূর্ণ ও পাহাড়িদের অধিকার বিরোধী বলে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়। এর ফলে অভ্যন্তরীণ সংঘাত ও সহিংসতা আরও বৃদ্ধি পায়।
বর্তমান বাস্তবতা লক্ষ্য করলে দেখা যায়, পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির পরও স্থায়ী শান্তি ফিরে আসেনি, দীর্ঘ প্রায় ২ দশকেরও বেশি সময় ধরে এখনো সংঘাত চলমান। পাহাড়ি জনগোষ্ঠী মনে করে, সেনাবাহিনীর উপস্থিতি তাদের স্বাভাবিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনকে ব্যাহত করছে। আবার সরকার মনে করে, সেনাবাহিনী না থাকলে সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর সহিংসতা বেড়ে যাবে এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতা হুমকির মুখে পড়বে।
এই ধরণের দ্বন্দ্বের কারণে “সেনা শাসনের প্রয়োজনীয়তা” নিয়ে পক্ষে ও বিপক্ষে বিতর্ক চলমান। বাস্তবে চুক্তির প্রতিশ্রুত রাজনৈতিক সমাধান ও আঞ্চলিক স্বশাসনের সুযোগ না দেওয়ায় সেনাবাহিনীকে বিকল্প শক্তি হিসেবে টিকিয়ে রাখা হয়েছে বলে পাহাড়িদের অনেকে মনে করেন।
ভবিষ্যতের সম্ভাবনা নিয়ে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, চুক্তি বাস্তবায়নের সীমাবদ্ধতাগুলো কাটিয়ে উঠা ছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে স্থায়ী নিরাপত্তা ও শান্তি প্রতিষ্ঠা কখনোই সম্ভব নয়। ভূমি বিরোধ মীমাংসা করতে হবে স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষভাবে, স্থানীয় জনগণের সাংস্কৃতিক ও জাতিগত পরিচয়কে সংবিধানিক স্বীকৃতি দিতে হবে, এবং আঞ্চলিক পরিষদকে প্রকৃত অর্থে ক্ষমতা প্রদান করতে হবে।
আঞ্চলিক অখন্ডতা ও নিরাপত্তা বজায় রাখার স্বার্থে সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি বেসামরিক প্রশাসনকেও শক্তিশালী করা গেলে দীর্ঘমেয়াদে সংঘাত হ্রাস পাবে বলে আশা করা যায়। অন্যদিকে পাহাড়ি রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর অভ্যন্তরীণ বিভাজন নিরসন না হলে শান্তি প্রক্রিয়া বারবার ব্যাহত হবে।
অতএব, ১৯৯৭ সালের শান্তি চুক্তি নিঃসন্দেহে একটি ঐতিহাসিক উদ্যোগ, যা পাহাড়ি জনগণের জন্য ন্যূনতম স্বীকৃতি ও আস্থার ক্ষেত্র তৈরি করেছে বলা যায়। কিন্তু এর অসম্পূর্ণ বাস্তবায়ন, রাষ্ট্রীয় কাঠামোর কড়াকড়ি, ভূমি সংক্রান্ত সমস্যা, এবং অভ্যন্তরীণ বিভাজনের কারণে চুক্তি যে প্রত্যাশিত শান্তি ও উন্নয়নের পথ প্রশস্ত করবে, তা এখনো বাস্তবে রূপ নেয়নি।
পাহাড়ি অঞ্চলের মানুষের নিরাপত্তা, মর্যাদা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার মধ্য দিয়েই এ চুক্তি পূর্ণতা পাবে, আর সেটিই হবে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ শান্তি ও সামাজিক সম্প্রীতির এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।
লেখক: ইরফান ইবনে আমিন পাটোয়ারী, শিক্ষার্থী, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।